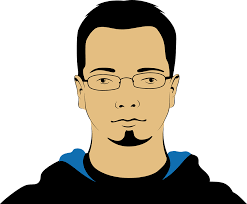
করোনা কালে এক বছর ঘরবন্দি। বেড়াতে যাওয়ার উপায় ছিল না মোটে। কিন্তু পর্যটনস্থলগুলি খুলে যেতেই আতঙ্কের সঙ্গে আপোস করে চলছে ছুটি কাটানো। এই সময়ে পাহাড়-পিপাসু মানুষের সেরা ঠিকানা হতে পারে রাজ্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফু। ভিড় নেই, করোনার প্রকোপ নেই, শুধু নিজে স্বাস্থ্যবিধি মানলেই সুস্থ ভাবে ঘুরে আসা যায় হাতের কাছে এই এলাকা থেকে। দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা।
ট্রেনের টিকিট কাটা হয়েছিল হঠাৎ। এক বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল উত্তরের উদ্দেশে। ঠান্ডা জাঁকিয়ে পড়ার আশঙ্কা। সব জেনেও ঠিক হল সান্দাকফু ওঠা হবে হেঁটে। সাধারণত সান্দাকফুর উদ্দেশে হাঁটা শুরু হয় মানেভঞ্জন থেকে। কেউ কেউ ধোতরে দিয়েও ওঠেন। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে মানেভঞ্জন যাওয়া হল গাড়িতে।
সান্দাকফু নিয়ে অনেক গল্পই শোনা। চোখের সামনে অমন করে কাঞ্চনজঙ্ঘার ‘ঘুমন্ত বুদ্ধ’ দেখতে পাওয়া যে সৌভাগ্যের ব্যাপার, যাওয়ার আগে সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন অনেকেই।বলেছিলেন, রহস্যে মোড়া থাকে উত্তরবঙ্গের এই পাহাড়ি রাস্তা। সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানের ভিতর দিয়ে যে পথ সান্দাকফু যায়, তাতে বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকে নানা আকর্ষণ।

টংলু
টংলু একটি ছোট্ট গ্রাম। একই রকম দেখতে কয়েকটি মাত্র বাড়ি। প্রায় সব ক’টিতেই পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। দু’দিকে পাহাড়ের উঁচু-নিচু পথ। মানুষজন বলতে মূলত পর্যটক আর হোটেলের মালিক-কর্মচারী। বেলা বাড়তেই মেঘে ঢেকে গেল এলাকা। যেন আকাশ নেমে এল মাটিতে। প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে মেঘের সারি এ পাশ-ও পাশ করতে লাগল। পর্যটকদের চোখে তখন বিস্ময়।
এখানকার সব ক’টি থাকার জায়গাতেই গরম জল, খাবার পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। বাহারি খাবার না পাওয়া গেলেও চা, কফি, আর তিনবেলা পেট ভরা নুডল্স, ভাত, তরকারি, ডিম, মাংস পেতে অসুবিধা হয় না। তবে উচ্চতার সঙ্গেই বাড়তে থাকে খাবারের দাম।
গাড়িতেও ওঠা যায় সান্দাকফু পর্যন্ত, কিন্তু হেঁটে ওঠার আনন্দ আলাদা। আর এই পথে হাঁটার অন্যতম শর্ত হল শারীরিক সক্ষমতা। কারণ, প্রথম বারের উৎসাহীদের জন্য অপেক্ষায় থাকে পাহাড়ের কাঠিন্য। মানেভঞ্জনে পৌঁছে তাই একজন অভিজ্ঞ গাইড খুঁজে নেওয়া দরকার। শেষ জনবসতি মানেভঞ্জনের পরে কোথাও কোনও বিপদ হলে রক্ষাকর্তা একমাত্র সেই সঙ্গীই।

গৈরিবাস
এ যাত্রায় যিনি পথ দেখালেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কলকাতা থেকেই। নাম পিটার রাই।মানেভঞ্জনের বাসিন্দা। মানেভঞ্জনে সময় নষ্ট না করে পিটারই পরামর্শ দিলেন সোজা টংলু চলে যেতে। এই পথে সাধারণত তিন জায়গায় রাত কাটানো হয়। প্রথম টংলু বা টুমলিং, পরের রাত কালিপোখরি এবং তার পরে সান্দাকফু। কোনও থাকার জায়গায়ই আগে থেকে ঠিক করা ছিল না। টংলুতে গিয়ে প্রথম রাত কাটল সেখানকার ‘ট্রেকার্স হাট’-এ।
দুপুর গড়াতেই সূর্যের তেজ পড়ে আসে। ঠান্ডা বাড়ে। ফলে দিন শেষ হলেই আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ঠান্ডা এতটাই। সূর্যাস্তের পরে সামান্যই আলো দেখা যায় এখানে। সবটাই চলে যে সৌরশক্তিতে। এখানে বিদ্যুতের সরবরাহ সর্বত্র নেই। এখানে রাতে খাওয়ার সময় হল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে। তার পরে আর নয়। ন’টার মধ্যে সব বন্ধ করে ঘরে ঢুকে যাওয়াই রীতি।
পরদিন সকালে টংলু থেকে রওনা দেওয়ার পালা। হেঁটে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে পৌঁছনো গেল গৈরিবাস। এই পুরো রাস্তাটির বেশির ভাগই নামার পথ। তাই হাঁটতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। তবে তখনও জানা ছিল না কী অপেক্ষা করছে আগামীর জন্য। ঝকঝকে রোদে দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যানগম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে। পথ চলতি কয়েক জনের সঙ্গে কথা হল, বেশির ভাগই কলকাতা ও তার আশপাশ থেকে এসেছেন। কিছু গাড়ি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। হাঁটা পথের পথিকেরা চলতে থাকল দুলকি চালে।

গৈরিবাস
পাহাড়ের বৃষ্টি বড় আকস্মিক হয়। তাই বৃষ্টিতে হাঁটার মতো ব্যবস্থা রাখা দরকার। ‘পঞ্চো’ বলে একটি রেনকোট জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা হয় এখানে। পিঠের ব্যাগ-সহ প্লাস্টিকের এই আবরণে ঢাকা পড়ে যায় শরীর। গৈরিবাসে কিছু ক্ষণের বিশ্রাম নেওয়াই চল। তার পরে আবার পথ চলা। এ বার সবটাই চড়াই। সফরের দ্বিতীয় দিনের পথের এই অংশ খানিক কঠিন। কিছুটা চলার পরে শহুরে পর্যটকেদের অবস্থা বুঝে বাধ্য হয়ে মাঝপথে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করলেন পিটার। এখানেই প্রথম মালুম হল, গাইড না থাকলে চলত না। পিটার ছিলেন, তাই এ যাত্রায় রক্ষা হল।
গাড়িতে সামান্য পথ। পৌঁছে যাওয়া গেল কালিপোখরি। রাত কাটবে স্থানীয় একজনের বাড়িতে। ততক্ষণে দেখা গিয়েছে ফোনের নেটওয়ার্ক প্রায় নেই বললেই চলে। চার্জও নেই। কাঠের দেওয়ালের বাড়ি। এখানে রয়েছে একটি ছোট্ট কালো জলাশয়। তার থেকেই জায়গাটির নাম হয়েছে কালিপোখরি।এখান থেকে ক্রমশ কাছে আসতে শুরু করে রূপসী কাঞ্চনজঙ্ঘা। সন্ধ্যার পরেই নামতে থাকে পারদ। কোনও কোনও দিন দেখা যায়, জলাশয়ে উপরের দিকটা ধীরে ধীরে জমে সাদাটে ভাব নেয়। দু’-তিনটে লেপ, ভিতরে সোয়েটারও যেন সেই ঠান্ডার সঙ্গে লড়তে অক্ষম ঠেকে।
তৃতীয় দিনটা আরও গুরুত্বপূরর্ণ। ওঠা পথের শেষ। দেখা যাবে সান্দাকফু। কালিপোখরি থেকে হাঁটা শুরু করা গেল পাহাড়ের কোল দিয়ে। দু’দিকে ঢালের মতো নেমে গিয়েছে উপত্যকা। ঝকঝকে আকাশ, রোদ জ্বলজ্বল করছে হিমালয়ের গায়ে। একপাশে পাহাড়ের রেখা কখনও দেখা দিচ্ছে, কখনও মিলিয়ে যাচ্ছে। সমতলের কোনও কিছুর সঙ্গেই যেন পাহাড়ের তুলনা টানা যায় না। তাই উপমা দেওয়া দুষ্কর। পথ চলতে চলতেই নজরে পড়তে থাকে বরফ। ‘তুষার’ বলা যায় একে। বরফ না পড়লেও শিশির ও রাস্তার জল জমে গুঁড়ো বরফ তৈরি হয়ে লেগে থাকে পাহাড়ের ঢালে। এ পথে কোথাও কোথাও চোখে পড়ে একটা-দুটো বাড়ি। ছোট্ট সংসার। যাপনের আদিমতম চাহিদাগুলি ছাড়া, এখানে প্রায় কিছুই নেই।
সান্দাকফু পৌঁছে যাওয়া গেল কয়েক ঘণ্টায়। আগের দুই রাত যে ভাবে কাটাতে হয়, তার তুলনায় এখানে ব্যবস্থাপনা খানিক উন্নত। তবে চারপাশের রূপ সেই ভাবনা থেকে সরিয়ে নেয় মন। চোখের সামনে তখন শুধুই কাঞ্চনজঙ্ঘা। কী বিশাল সেই চেহারা। যেন কোনও শিল্পী হাতে করে পাহাড়ের গায়ে লেপে দিয়েছেন দুধরঙা বরফ। দেখে মনে হয়, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে বুদ্ধের ঘুমন্ত হৃদয়। ধর্মতলা, কলেজ স্ট্রিট, গড়িয়াহাট ফেরত শহুরে বাঙালির কাছে এ দৃশ্য রীতিমতো বিস্ময়ের। কী শক্তিতে বিধাতা গড়েছেন এমন প্রকৃতি! মনে হয়, শত যোজন দূরে থাকা পাহাড় গাল ঠেকিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফুর সঙ্গে। দূরে দেখা যায় এভারেস্ট, মাকালুর মতো বইয়ে পড়া পাহাড়ের শ্বেতশুভ্র সব শৃঙ্গ।
এখানেও থাকার জায়গা ‘ট্রেকার্স হাট’। সেখানে নিজেদের তিন বিছানার কোনার ঘরে কোনওমতে ব্যাগ রেখে রওনা দেওয়া গেল ভিউ পয়েন্টের উদ্দেশে। পাহাড়ের দিকে চেয়ে বসে কেটে যেতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।
যদি প্রথাগত পর্যটকের মতো মন চায় বেড়াতে গিয়ে কেনাকাটা করা এবং চারটে দর্শনীয় স্থান দেখা, তবে সান্দাকফু তালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভাল। আর ইচ্ছা যদি থাকে প্রকৃতির কোলে কয়েকটি দিন কাটানো, তবে এ জায়গা আপন করে নেয় তাঁকে। বিলাসবহুল থাকার ব্যবস্থা নেই, তবে পাহাড় তা নিয়ে মন খারাপ করার সুযোগও দেয় না। নিরিবিলিতে কয়েকটা দিন কাটাতে চাইলে সান্দাকফু বারবার ডাকবে শহুরে পর্যটককেও।